নৈতিক তত্ত্বসমূহ প্রশ্ন উত্তর
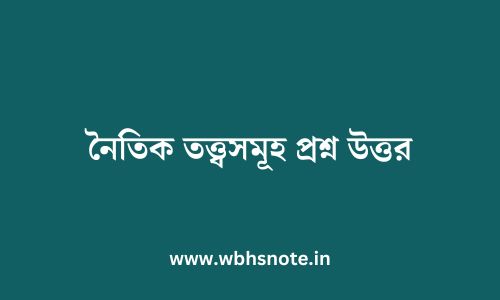
১। ফলমুখী বা উদ্দেশ্যমুখী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
ফলমুখী বা উদ্দেশ্যমুখী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য
যে মতবাদ অনুসারে কোনো কাজের নৈতিক মূল্য সেই কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তাকে উদ্দেশ্যমুখী বা ফলমুখী তত্ত্ব বলা হয়। ফলমুখী নৈতিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-
(1) নৈতিকতার মানদণ্ড ফলাফল: এই মতবাদ অনুসারে কোনো কাজ নৈতিক নাকি অনৈতিক তা নির্ভর করে কাজটির ফলাফলের উপর। যে কর্মের ফল ভালো সেই কাজটি নৈতিক এবং যার ফল মন্দ সেই কাজটি অনৈতিক।
(2) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নৈতিকতা: কোনো কাজের উদ্দেশ্য কী তার দ্বারাই সেই কাজের নৈতিকতা নির্ভর করে। কাজের উদ্দেশ্য ভালো হলে কাজটি নৈতিক হয় এবং উদ্দেশ্য মন্দ হলে কাজটি অনৈতিক হয়। এক্ষেত্রে কাজটির পদ্ধতির উপর তার নৈতিকতা নির্ভর করে না।
(3) নমনীয়তা: উদ্দেশ্যমুখী নৈতিক মতবাদ অনুসারে পরিস্থিতি ও ফলাফলের ভিত্তিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকে। এক্ষেত্রে স্থির ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলে কিছু নেই।
(4) উপাযাগিতা : ফলমুখী নৈতিকতার একটি রূপ হল উপযোগিতা। এই নীতি অনুসারে কোনো একটি কাজ নৈতিকভাবে সঠিক যখন তা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ বা আনন্দ সৃষ্টি করে।
(5) সুখবাদ : ফলমুখী নৈতিকতার অন্যতম একটি রূপ হল সুখবাদ। এই নীতি অনুসারে কোনো একটি কাজ নৈতিকভাবে সঠিক যখন তা কষ্টের পরিবর্তে সুখ ও আনন্দের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।
২। সুখবাদের হেঁয়ালি বা আপাত বিরোধটি আলোচনা করো।
যে মতবাদ অনুসারে সুখ জীবনের পরম কাম্য, সেই মতবাদকে সুখবাদ বলে। সুখদায়ক কাজই হল ভালো কাজ; যে কাজ সুখ উৎপাদন না করে দুঃখ সৃষ্টি করে সেই কাজ মন্দ কাজ।
সিজউইক (Sidgwick) মনে করেন, সুখবাদের উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আপাত বিরোধ (Paradox)। মানুষ যতই সুখের পশ্চাতে ছুটে যায়, সুখ ততই আলেয়ার মতো দূরে চলে যায়। সুখের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে আলেয়ার মত অন্ধকারে পথিককে বিভ্রান্ত করার আহ্বান। নিরলস সুখের অনুসন্ধান হতাশায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বল্লাহীন উচ্ছৃঙ্খল সুখের অনুসরণ মানুষকে স্থায়ীভাবে তৃপ্ত করতে পারে না। ইন্দ্রিয় সুখভোগে মানুষ একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই সিজউইক বলেন-
“সুখের প্রতি আকর্ষণ যত বেশি হবে, ততই মানুষ সুখলাভে ব্যর্থ হবে। সুখ পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল সুখকে ভুলে যাওয়া।”
অবশ্য র্যাশডল (Rashdall) মনে করেন, সুখবাদের বিরুদ্ধে সিজউইকের এই অভিযোগ অতিরঞ্জিত। সবক্ষেত্রে পূর্ব থেকে হিসেব করে সুখের অনুসন্ধান করলে সুখকে হারাতে হবে বা সুখ কমে যাবে- এ কথা ঠিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হিসেবের ফলে অধিক পরিমাণ সুখপ্রাপ্তি ঘটতে পারে।
মন্তব্য
উপসংহারে বলা যায় যে নিরলস সুখের অনুসন্ধান মানুষের শান্তি নষ্ট করে। মানুষের প্রকৃতিতে আছে বিচারবুদ্ধি। নির্বিচারে সুখের অনুসন্ধান করলে প্রকৃতি তাকে বাধা দেয়, সুখ পেতে হলে সংযত হতে হবে। সিজউইক তাঁর বক্তব্যে এই সত্যই তুলে ধরেছেন।
৩। নৈতিক আত্মসুখবাদ-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
নৈতিক আত্মসুখবাদ -এর মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল-
- কোনো ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যতাবোধ বা কর্তব্য হল নিজের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ উৎপাদন করে কর্ম করা।
- নৈতিক আত্মসুখবাদীর, সাধারণ অর্থে শুধুমাত্র স্বার্থপর (Selfish) বা নিছক আত্ম-সর্বস্ব (Egotist) হওয়ার প্রয়োজন নেই।
- নৈতিক আত্মসুখবাদীরা নিজ স্বার্থে পরার্থবাদ (Altruism) প্রচার করতে পারে।
- অপর ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কর্ম আত্ম কল্যাণের জন্য- এই প্রকার বিবেচনা নৈতিক আত্মসুখবাদ বা স্বার্থবাদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয়।
- কেবল নিজ ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা তার আত্মকল্যাণের অনুকূল হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্তা অন্য ব্যক্তির পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা ও বিচারক হয়।
৪। মিল ও বেখামের উপযোগবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক বিচার করা হয় যে মানদণ্ড অনুযায়ী তাকে বলে নৈতিক বিচারের মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের স্বরূপ সম্পর্কে নীতিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আত্মসুখবাদের বিপরীত মতবাদ হল পরসুখবাদ বা উপযোগবাদ (Utilitarianism)। আত্মসুখবাদে নিজের সুখের কথা বলা হয় কিন্তু পরসুখবাদ বা উপযোগবাদে কেবলমাত্র নিজের সুখ নয়, সকলের জন্য সুখ কামনা করার কথা বলা হয়। সেই কারণে পরসুখবাদে-‘সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ’ (The greatest happiness of the greatest number) – এটিকে জীবনের নৈতিক আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।
এই মতবাদে কাজের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুখের পরিবর্তে সার্বিক সুখকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই উপযোগ নীতি অনুসারে বলা হয়, আমাদের সেই নৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করে কাজ করা উচিত যে কাজটি মন্দ বা অমঙ্গলের তুলনায় সর্বাধিক মঙ্গল ও কল্যাণ উৎপন্ন করবে। সাধারণের সর্বাধিক মঙ্গলবিধান করে যে কাজ সেই কাজই হল যথোচিত কাজ। যে কাজের পরিণতি বা ফল সর্বসাধারণের আনন্দ উৎপন্ন করে কেবল তারই নৈতিক মূল্য আছে। এই নৈতিকতা হল ফলমুখী নৈতিকতা।
উপযোগবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীতিবিদ ফ্র্যাঙ্কেনা (Frankena) বলেছেন, উপযোগবাদ বলতে সেই মতবাদকে বোঝায় যেখানে বলা হয়, কোন্ কাজটি ন্যায়, কোন্টি অন্যায় তা বিচার করা বা কোন্ কাজটি করতে আমরা নীতিগতভাবে বাধ্য তা নির্ণয়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড হল উপযোগ নীতি। উপযোগবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জেরেমি বেথাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল। এ ছাড়া দার্শনিক হেনরি সিজউইক হলেন এই মতবাদের অন্য এক সমর্থক। উপযোগবাদ সম্পর্কে বেথামের মতবাদকে বলা হয় স্থূল বা অসংযত উপযোগবাদ (Gross or Unrefined Utilitarianism)।
৫। উপযোগবাদের মূল নীতিগুলি বিশ্লেষণ করো।
নীতিবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য হল নীতি ও আদর্শের মানদণ্ডে সামাজিক মানুষের আচরণের নৈতিক বিচার করা। এই বিচার উচিত-অনুচিত, ভালো- মন্দ প্রভৃতি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেসব মানদন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচার করা হয় তাকে নৈতিক আদর্শ বলে। নীতিবিদ্যার বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে উপযোগবাদ অন্যতম। উপযোগবাদের মূল নীতিগুলি হল-
- সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করা আমদের জীবনের নৈতিক আদর্শ।
- আমাদের কর্তব্য কেবল নিজের সুখ উৎপাদন করা নয়, অপরের সুখ উৎপাদন করা বা কামনা করাও আমাদের নৈতিক কর্তব্য।
- বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় অর্থাৎ বহুমানুষের সুখ ও কল্যাণ সাধনের দ্বারাই ব্যক্তি সর্বাধিক সুখ ও আনন্দ পেতে পারে।
- যে কাজ সর্বসাধারণের বা বহুজনের সুখ উৎপাদনের উপযোগী সেই কাজ যথোচিত বা ভালো কাজ। যে কাজের দ্বারা সর্বসাধারণের সুখ উৎপাদন করা যায় না বা সাধারণের সুখলাভের পরিপন্থী তা অনুচিত বা মন্দ কাজ। তাই কাজের উপযোগিতা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি।
- সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি।
- সুখ লাভই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিজের সুখ ও অপরের সুখের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নয়।
- সুখের মাপকাঠি হল সুখের পরিমাণ। নিজের সুখের পরিমাণ অপেক্ষা অপরের সুখের পরিমাণ বেশি হলে অপরের সুখ কামনা বা অনুসন্ধান যুক্তিসম্মত।
৬। কর্ম উপযোগবাদের মূল বক্তব্যটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
কর্ম উপযোগবাদ অনুসারে, কোনো বিশেষ কাজ যে ঠিক বা উচিত কাজ তা সরাসরি তার উাপযোগিতা অনুসারেই নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ কাজ ঠিক বা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে ব্যক্তিকে
এটাই দেখতে হবে যে ওই বিশেষ কাজটি ওই পরিস্থিতিতে অন্যান্য কাজ অপেক্ষা জগতে অকল্যাণের চেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন করতে পারে কিনা। কর্ম উপযোগবাদীদের মতে, কোনো বিশেষ কাজ কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা বেশি কল্যাণ সাধন করতে পারলে সেই কাজটি হবে ঠিক বা উচিত কাজ আর ওই পরিস্থিতিতে কাজটি জগতে অকল্যাণের তুলনায় বেশি পরিমাণে কল্যাণ সাধন না করতে পারলে কাজটি হবে বেঠিক বা অনুচিত কাজ। সংক্ষেপে বলতে গেলে কর্ম উপযোগবাদীদের মতে কোনো বিশেষ কাজ বহুজনের উপযোগী বা উপকারী হলে নৈতিক বিচারে তা ‘সৎকাজ’ বা ‘উচিত কাজ’ বলে বিবেচিত হবে।
কর্ম উপযোগবাদী কোনো বিশেষ কর্মের উপযোগিতাই কেবল নির্ধারণ করেন, কর্মনীতি বা নিয়মের নয়। বিশেষ কোনো কর্মের পরিণাম বিচার করেন, কোনো কর্মনীতি বা নিয়মের পরিণাম নয়। স্পষ্টতই কর্ম উপযোগবাদে কর্মটাই প্রধান্য পায়, কর্মনীতি নয়। জেরেমি বেথাম, জি ই ম্যুর এবং সম্ভবত মিল এই প্রকার অভিমত পোষণ করেন।
কর্ম উপযোগবাদ বিশেষ কোনো কাজের সম্ভাব্য পরিণতিগুলিকে জানতে চায়। অর্থাৎ জানতে চায় যে, অপারপর ব্যক্তি ওই বিশেষ কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি কাজটি করে তাহলে তাতে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিনা। বিশুদ্ধ কর্ম উপযোগবাদের সার কথা হল- কর্মনীতির ওপর নির্ভর না করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কাজের পরিণতি কী হতে পারে তা বিবেচনা করেই কাজটি করতে হবে। জিয়া
৭। নীতি উপযোগবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
অথবা, নৈতিক মতবাদরূপে নীতি উপযোগবাদের ব্যাখ্যা করো।
নীতি উপযোগবাদের সার কথা হল কোনো কর্মের নৈতিক বিচার কর্মনীতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। বিশপ বার্কলে থেকে ব্রান্ডট্ পর্যন্ত অনেক চিন্তাবিদ এই মতবাদ সমর্থন করেন। মিল তাঁর উপযোগবাদের বিভিন্ন স্থানে নীতি উপযোগবাদকে সমর্থন করেছেন।
এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, কোন্ নিয়মের ভিত্তিতে কাজ করলে সর্বাধিক হিতসাধন হবে তা নির্ণয় করা। এই তত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়মের অবস্থান। এই মতের সাধারণ কথা হল -সর্বক্ষেত্রে না হলেও বিশেষ অবস্থায় করণীয় ক্রিয়ার নৈতিক বিচার নিয়মের ওপর নির্ভর করে। সবসময় আমাদের নিয়ম স্থির করতে হবে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে যে ‘কোন্ নিয়ম সকলের জন্য সর্বাধিক হিতসাধন করবে?’ তবে নিয়মকে অবশ্যই উপযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে, পরিচ্ছন্ন, পুননির্মাণ করতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে।
নীতি উপযোগবাদ তত্ত্বটি কর্ম উপযোগবাদ তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। কর্ম উপযোগবাদে যেখানে কোনো একটি কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মটির ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হয়, সেখানে কর্মনীতি প্রাধান্য পায় না; ঠিক তেমনই নীতি উপযোগবাদ অনুসারে কর্মের ফলাফলের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বরং কর্মনীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্ম উপযোগবাদে ফলমুখী নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও নীতি উপযোগবাদে নিয়মভিত্তিক নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতি উপযোগবাদীগণ মনে করেন যে কর্মনীতি ছাড়া কোনো কর্মের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়।
৮। চরমপন্থী ও নরমপন্থী কর্তব্যবাদের মূল বক্তব্য আলোচনা করো।
কর্তব্যবাদ সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলিকে চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
চরমপন্থী কর্তব্যবাদ
চরমপন্থী কর্তব্যবাদ অনুসারে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে পৃথকভাবে আমাদের নির্ধারণ করতে হয় কোন্ কাজটি ন্যায়সংগত এবং কোল্টি নয়। যেটি ন্যায়সংগত তা করতে আমরা নীতিগতভাবে বাধ্য। এই মতবাদ অনুসারে, আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য কোনো কর্মনীতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। চরমপন্থী কর্তব্যবাদীরা বলেন, এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই যা সমস্ত পরিস্থিতি নির্বিশেষে কর্তব্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে। ‘সর্বদা সত্য কথা বলা’, ‘প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা’ ইত্যাদি সার্বিক নিয়ম বলে কিছু নেই। সমস্ত ঔচিত্যমূলক অবধারণই হল বিশেষ অবধারণ। জোসেফ বাটলার একজন চরমপন্থী কর্তব্যবাদী।
নরমপন্থী কর্তব্যবাদী
নরমপন্থী কর্তব্যবাদ অনুসারে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির বিচার করে আমাদের মধ্যে ঔচিত্য সম্বন্ধে একপ্রকারের বোধ জন্মায়। নৈতিক বোধের উপর ভিত্তি করে কোন্ কর্মনীতি গঠন করা সম্ভব হতে পারে এবং সেই নীতি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে কোন্ কর্মটি করা উচিত ও কোল্টি অনুচিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব। নরমপন্থী কর্তব্যবাদীরা বলেন, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ কাজটি করণীয় ও কোল্টিন্ট নয় তা নির্ধারণ করার জন্য স্বজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হয়। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি তার স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তার উচিত কর্ম কী হবে তা নির্ধারণ করতে পারে। সেই বিষয়ে কোন্ট করা উচিত তাই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হবে।
৯। “কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য” কান্টের এই নীতিটি ব্যাখ্যা করো।
‘কর্তব্যের জন্য কর্তব্য’ কান্টের এই নীতিতত্ত্বটি, নীতিদর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কান্ট-এর মতে ‘কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য’ এটি একটি সার্বিক ও নৈতিক নিয়ম। এই কথাটির মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ দায়িত্ববোধকে জাগরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কান্টের মতে এই নিয়ম দেশ-কালভেদে সর্বত্র সার্বিকভাবে এবং সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।
(1) কর্তব্য পালন হল অন্তরের অনুভূতি: কান্টের মতে মানুষকে বলপূর্বক কর্তব্য পালন করানো যায় না, কর্তব্য পালন করতে হয় অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। মন থেকে কেউ যদি মনে করে, কর্তব্য পালন করতে হবে বা কর্তব্য পালন করা উচিত তবেই সেই কর্তব্য সঠিক বা যথোচিতরূপে বিবেচিত হয়।
(2) কর্তব্য পরিচালিত হয় সদিচ্ছার দ্বারা: মানুষের সদিচ্ছা দ্বারা কর্তব্য পালিত হয়। সদিচ্ছা না থাকলে কর্তব্য পালন হয় না। কান্টের মতে ইচ্ছা যখন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেই ইচ্ছাকে বলা হয় সদিচ্ছা (সৎ+ ইচ্ছা)।
(3) কর্তব্যযুক্ত কাজ নৈতিকভাবে মূল্যবান: কান্টের মতে কর্তব্যহীন কর্মের তুলনায় কর্তব্যযুক্ত কাজ অনেক বেশি সুন্দর এবং নৈতিকভাবে মূল্যবান।
(4) কর্তব্য হল নিঃশর্ত আদেশ: কান্টের মতে, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালন করা- এটা হল এক শর্তহীন আদেশ। এই আদেশ পালনের মধ্যে কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে না। বিবেকের নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্তব্য সাধন করা হয়। এই আদেশ নৈতিক কর্তাকে কোনোরকম ফললাভের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবলমাত্র নৈতিক নিয়মের স্বার্থে নৈতিক নিয়ম পালনের সুযোগ দেয়।
পরিশেষে বলা যায়, ‘কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য’- কান্টের এই ধারণাটি নীতিদর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।
১০। কান্টের নীতি কর্তব্যবাদের সমালোচনা ব্যাখ্যা করো (ফ্র্যাঙ্কেনার মতে)।
অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেনা কান্টের নৈতিক মতবাদকে সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে পারেননি নিম্নলিখিত কারণে-
- প্রথমত: কান্টের নীতি কর্তব্যবাদ ‘কর্তব্যের দ্বন্দ্ব’ থেকে মুক্ত নয়। কান্ট অদ্বৈতবাদী নীতি কর্তব্যবাদের পৃষ্টপোষক হলেও সার্বভৌম নিঃশর্ত অনুজ্ঞার অন্তর্গত একাধিক কর্মনীতির উল্লেখ করেছেন। কর্মনীতি একাধিক হলে তাদের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দুটি প্রচলিত কর্মনীতি যদি এমন হয় যে তাদের একটিকে রক্ষা করতে গেলে অন্যটি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কোন্ কাজটি উচিত আর কোন্ কাজটি অনুচিত তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- দ্বিতীয়ত: কান্ট যে নৈতিক মানদণ্ডের উল্লেখ করেছেন তা প্রয়োগ করে কতগুলি কাজকে কর্তব্যকর্ম বলে গ্রহণ করা গেলেও মানদণ্ডটি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না।
- তৃতীয়ত: কান্ট প্রদত্ত মানদণ্ডে কোনো নিয়ম উত্তীর্ণ হলেই বলা যাবে না যে নিয়মটি অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য অর্থাৎ নিয়মটি নৈতিক। কোনো নিয়ম সার্বত্রিকরূপে চিন্তা করা গেলেও সেই নিয়ম অনুসারে কর্ম কর্তব্যকর্ম নাও হতে পারে। কান্টের সার্বত্রিক নিয়ম সম্পর্কে তাই অনেকে অভিযোগ করেন যে, কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মটিও কর্তব্যনিয়ম নয়। প্রসঙ্গত ফ্র্যাঙ্কেনা বলেন যে, কোনো নিয়মকে নৈতিক হতে গেলে নিয়মটি সার্বিক হওয়া এবং ‘সংগতিপূর্ণ’ হওয়া-ই যথেষ্ট নয়। নৈতিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন হয় আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত উপযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি। কাজেই কান্ট এবং তাঁর সমর্থকরা কর্মকে কেবল নিয়মভিত্তিক করে ‘কর্মের’ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেও ‘নৈতিক কর্মের’ বা কর্তব্যের কোনো সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।
Also Read – The Garden Party questions and answers