প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা | ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার বাংলা | Prodotto onuccheder vittite probondho rochona | Class 12 Bengali 4th Semester
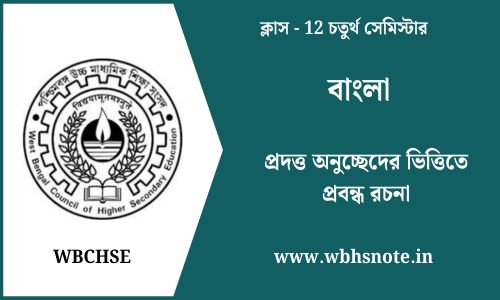
প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা লেখার নিয়ম
কোনো একটি বিষয়ে কোনো একজন লেখকের লেখার একটি অংশ দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি হল রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা। এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকাটিকে অবলম্বন করে পরীক্ষার্থী বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করবে এবং পরিণতি মান করবে।
এই ধরনের প্রবন্ধ লেখার আগে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে-
- প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে মূল রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে পরবর্তী অংশে সেই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- প্রবন্ধ রচনার সময়ে মূল লেখাটি যে গ্রন্থের অন্তর্গত, তা পড়া না থাকলেও অসুবিধা নেই।
- প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা যাবে।
- প্রবন্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- সমাজ-সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকারের পথগুলিও উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধের শব্দসীমার প্রতি অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।
১। [ছাত্রসমাজ দেশের আগামী প্রজন্ম, আগামী দিনের কর্ণধার। ছাত্ররা শৃঙ্খলাপরায়ণ হলেই আগামী দিনগুলি সুশৃঙ্খল হবে। ছাত্ররা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাদের রুচিবোধ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হবে। তারা সবার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে। তারা যৌবনশক্তি, দেশবাসীর পথপ্রদর্শক। তাদের সংযত জীবন নিজেদের যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমন দেশবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করবে।]
শৃঙ্খলাবোধ ও ছাত্রসমাজ : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ গঠনের প্রধান স্তর। প্রতিটি ছাত্র ভবিষ্যতে দেশের সুনাগরিক হয়ে উঠবে। সেজন্য ছাত্রজীবনকে কোনোভাবে অবহেলা করা চলবে না। ছাত্রেরা জাতির চোখের মণি, বুকের ভরসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। তাদের মনে রাখতে হবে অধ্যয়ন ছাত্রজীবনের প্রধান তপস্যা। এই প্রসঙ্গে একটি সংস্কৃত শ্লোক অবশ্যই স্মরণে রাখা উচিৎ, “ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপ।” কঠোর শৃঙ্খলা ছাত্রকে যেমন সাফল্যের শীর্ষ মিনারে পৌঁছে দিতে পারে তেমন তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ও সৃষ্টি করতে পারে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে না। অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয় তাদের মধ্যে সৎ চিন্তাদর্শ সৃষ্টি করবে। সম্ভাবনা সঞ্জাত ছাত্রদল তখন নির্দ্বিধায় সত্যপন্থা অবলম্বনকে জীবনের আদর্শ বলে গণ্য করবে।
জ্ঞানের পিপাসা ছাত্রজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথার্থ জ্ঞানে পুরাতন মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েও নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা তারা অর্জন করবে। তাদের জীবনের একমাত্র সাধনা মনুষ্যত্ব অর্জন করা। আর সেই মনুষ্যত্ব তাকে শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেবে। মানবজীবন গঠনের প্রাথমিক সোপান শৃঙ্খলা। সহবত শিক্ষার অভাব ঘটলে ছাত্র উদ্ধত স্বভাবের হবে- গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না আর সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীলও হবে না। অথচ ছাত্রজীবন মনুষ্যত্ব অর্জন ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের যথার্থ সময়। এ সময় বিনয়ী হয়ে শিক্ষক-গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের অকৃপণ স্নেহের দানে জ্ঞানের সম্পদ ও হৃদয় উজাড় করা আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে।
জাতির জীবনে ছাত্রসমাজ ‘আশা-আকাঙ্ক্ষা-শক্তি’র ত্রিবেণি সঙ্গম। সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশের অগণিত মানুষের দুর্গতি মোচন করে এক আনন্দময় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব ছাত্রজীবন থেকে গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবা শিক্ষারই অঙ্গীভূত। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি ও কুসংস্কারে সমাজের বৃহত্তর অংশ পীড়িত। অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান জাতিকে শিক্ষার আলোকে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য। ছাত্রজীবনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সার্বিকভাবে না হলেও এককভাবে এই দায়িত্ব পালন করা যায়। এই দায়িত্বপালনই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের জন্ম দেবে।
ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ ও জাতির স্রষ্টা। সাধারণ মানুষকে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। রক্তদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে ‘রক্তদান শিবির’ আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দেশ বা জাতি যেখানে কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জর্জরিত ও কলুষিত সেখানে ছাত্রসমাজকে নীরব থাকলে চলবে না। অধ্যয়ন অবশ্যই ছাত্রদের কাছে মুখ্য, তা বলে সামাজিক দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যাবে না এবং সেক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে তাদের শৃঙ্খলাবোধ।
বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চা ছাত্রজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান শিক্ষায় খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। “Play is nature’s method of preparing mind and body.” খেলাধুলা মস্তিষ্ক থেকে কুচিন্তাকে দূর করে। কেবল শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য নয়, মনের বিকাশসাধন এবং সুস্থ বিনোদনের জন্যেও খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছাত্রজীবন থেকে নিয়ম ও শ্রমের মর্যাদা, সময়ের মূল্য, বন্ধুত্ববোধ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারা যায়। শিক্ষা যেমন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের রূপরেখা প্রস্তুত করতে সাহায্য করে- জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে, খেলাধুলাও সেরকম সাহায্য করে। খেলোয়াড়সুলভমনোভাব জাগ্রত হলে ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ জীবনে দৃঢ় ও অনমনীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও খেলাধুলা একে অপরের পরিপূরক। খেলাধুলা সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহযোগিতা করে। এই খেলাধুলার মাধ্যমেও তার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা সক্রিয় হয়ে উঠবে।
শিক্ষা যেমন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের রূপরেখা প্রস্তুত করতে সাহায্য করে – জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে, খেলাধুলাও সেরকম সহায়তা করে। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব জাগ্রত হলে ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ জীবনে দৃঢ় ও অনমনীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও খেলাধুলা একে অপরের পরিপূরক। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে দৈহিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। কেবল পুথিগত বিদ্যা অর্জন করলে চলবে -না, সেই বিদ্যার বিশাল বোঝা বহন করার জন্য লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে * খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরগঠনও একান্তই আবশ্যিক। দেশের মনীষীগণও খেলাধুলার অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পড়াশোনা ও খেলাধুলার মেলবন্ধনে ছাত্রেরা জড়তা-আলস্য কাটিয়ে উঠবে, অন্তরের জ্ঞানে জাগ্রত হবে আর তবেই তারা জীবনে সাফল্য লাভ করবে। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষাক্রমে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীর চরিত্রে শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি করতে সবথেকে বেশি কার্যকর।
২। [জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেইদিন হইতে জীবনের ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেইদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবে।
দ্রোণাচার্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘গাছের উপর যে পাখিটি বসিয়া আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখি কি দেখিতে পাইতেছ?’-অর্জুন উত্তর করিলেন, ‘না, দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।’ এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বিঘ্ন বাধার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবে।
তবে সেই লক্ষ্য কি? লক্ষ্য; শক্তি সঞ্চয় করা, যাহার দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।
জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি-সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টার দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনোরূপ সঞ্চয় করে না, সে পরমুখাপেক্ষী, সে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।
যে সঞ্চয় করিয়াছে সে-ই শক্তিমান, সে-ই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিবে।]
অধ্যবসায় : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
‘কেউ হতে চায় ডাক্তার, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার, আমি শুধু বোকাই হব, এটাই আমার অ্যাম্বিশন।’ জীবনমুখী গানের গায়ক যখন গেয়ে ওঠেন এই গান, তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না মহৎ পেশা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এসে বেশিরভাগ মানুষের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচুর অর্থ উপার্জন। সেই অর্থে ‘মুনাফাবাজ’ না হয়ে ‘বোকা’ বা সাধারণ মানুষ হয়ে থাকাটাই তার লক্ষ্য। তবে এ কথা ঠিক ছাত্রজীবনে একটা লক্ষ্য রেখে এগোনো উচিত, কারণ লক্ষ্যহীন জীবন হাল ছাড়া নৌকার মতো। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য ছাত্রজীবন থেকেই অধ্যবসায় প্রয়োজন।
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে কান্ডারি ছাড়া নৌকার মতো ঘুরে বেড়ানো অর্থহীন। দৃঢ় সংকল্পই হবে সেই জীবনপথের নাবিক। তবে জীবনের সাধনাকে সফল করে তুলতে হলে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে ক্রমাগত চেষ্টা ও অবিরাম উদ্যোগ নিতে হবে। এই চেষ্টাই অধ্যবসায়।
‘Failure is the pillar of success’ অর্থাৎ ব্যর্থতা থেকেই জীবনে সাফল্য আসে। আর অধ্যবসায় এই সফলতার পথকে আরও প্রশস্ত করে। এটি একটি চারিত্রিক গুণ; যে গুণবলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। আগুন জ্বালানো শেখা থেকে মানুষ পরিশ্রম করে আসছে। পরিশ্রমের জন্যই মানুষ আজ মহাকাশে পাড়ি দিতে পেরেছে। মানুষের বসবাসের অযোগ্য পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করে তুলেছে সে নিজ চেষ্টাতেই। বড়ো বড়ো শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, পরিশ্রমের মাধ্যমেই নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। কোনো লক্ষ্যপূরণ নির্দিষ্ট সাধনাপথ ব্যতীত সফল হয় না। যেমন পরমাণু বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম ভারতের ‘মিসাইল ম্যান’ নামে পরিচিত। কিন্তু ছেলেবেলায় তিনি চরম দরিদ্রতার মধ্যে বড়ো হয়েছেন। কমবয়স থেকেই তাঁর কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব ছিল। সেইরকম পরিবেশে বড়ো হয়েও তিনি নিজের চেষ্টা ও সাধনায় একাধারে অধ্যাপক, লেখক, বিমান প্রযুক্তিবিদ এমনকি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
অধ্যবসায়ের অভাবে জীবন হবে নিরর্থক। প্রতিটা মানুষের মধ্যেই কোনো-না-কোনো প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সেই প্রতিভা খুঁজে নিয়ে মানুষকেই দৃঢ় মনোবল নিয়ে জীবনে অগ্রসর হতে হবে। নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য তাই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কেবল আবেগ, শখ বা ভালোলাগা নয়; অধ্যবসায়ের জন্য চাই প্রবল ইচ্ছা এবং কঠোর পরিশ্রম।
ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। পরবর্তীকালে তারাই এই দেশকে পরিচালনা করবে। তাই তাদের তারুণ্যকে কাজে লাগিয়ে অধ্যবসায়ে মন দিতে হবে। অনেক সময় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হলে তারা হতাশায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেই ব্যর্থতা থেকেই তারা জীবনে সফল হবে। তাই সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তাদের অধিক অনুশীলনে উৎসাহ দিতে হবে।
জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথে আসবে নানা বাধা, কিন্তু সেইসব প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আমরা অধ্যবসায় চালিয়ে যাব। প্রথমেই বৃহৎ কোনো লক্ষ্যমাত্রা না রেখে ছোটো ছোটো লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে এবং সফলতা আসার পর পরবর্তী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এইভাবে আমরা নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে অভীষ্টে পৌঁছে যাব। তাই সকলকেই এই বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে দেশের অগ্রগতিতে নিজেকে একজন অংশীদার করে তুলতে হবে। কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হবে-
“পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার…. পারো কি না পারো করো যতন আবার একবার না পারিলে দেখো শত বার।”
৩। [জন্মমুহূর্ত থেকেই মানুষের চলা সময়ের পথ ধরে। স্বল্প জীবনপরিধির মধ্যে মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে মূল্যবান সময়কে ব্যবহার করতে হবে সঠিকভাবে।
সময়ের গুরুত্ব: ক্ষণস্থায়ী জীবনে অনেক বাধা আছে। তাই কর্তব্যপালন একান্ত জরুরি। জীবনে সময়ের অপব্যবহার রোধ করে জীবনেরই মূল্যবৃদ্ধি করা প্রয়োজন; কারণ কোনো মূল্যের বিনিময়ে সময় কেনা যায় না। যারা জীবনে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন তারা আজও স্মরণীয়, বরণীয়।
ছাত্রজীবন থেকেই সময়নিষ্ঠার প্রশিক্ষণ: বাল্যকাল থেকেই সময়নিষ্ঠার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কারণ সব উন্নতির মূলে আছে সময়নিষ্ঠা। এর মাধ্যমে জাগে কর্তব্যবোধ, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতাবোধ।
সকলেরই হাতে থাকে সময়ের অমূল্য সম্পদ। সময় সম্পদই সুখশান্তির পথ প্রশস্ত করে জীবনকে উজ্জ্বল করে।]
সময়ের মূল্য ও সময়ানুবর্তিতা : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
‘এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূরবিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই, একবারও তাহার জন্য দুঃখ করি না।’- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বক্তব্য শিরোধার্য করে বলা যায়, সময়ের স্বত্ব অনায়াসে ত্যাগ করার জন্য আমাদের দুঃখ পাওয়া উচিত। কেন-না জন্ম থেকেই মানুষকে চলতে হয় মহাকালের পথ ধরে, কিন্তু মহাকালের কাছে মানুষের জীবন নিতান্তই ছোটো। অথচ মানুষের এই ছোটো জীবনে কত স্বপ্নের ছবি ভিড় করে থাকে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে মানুষের জীবনে চাই নির্দিষ্ট সময়। তাই সময়ের মতো মূল্যবান মনুষ্যজীবনে আর কিছু হয় না। যেহেতু ‘সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়’, তাই প্রতিটি জীবনে সময়ানুবর্তিতার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।
সময়ের বিরাট প্রবাহের তুলনায় মানুষের আয়ু খুবই সামান্য, তাই এই জীবনের প্রতি মানুষের কর্তব্যপালন একান্ত জরুরি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। যে মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন, সে মানুষের কাছে সময় অপচয় মৃত্যুর শামিল। জ্ঞানী ও মহান মানুষ সম্পর্কে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাঁরা প্রত্যেকেই সময়কে কাজে লাগিয়ে সময়ের অপব্যবহার রোধ করে জীবনেরই মূল্য বাড়িয়েছেন। গুণী মানুষেরা তিল তিল করে সময়কে কাজে লাগিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক-একটি পিরামিড গড়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বই বাঁধাইয়ের দোকানের কিশোর কারিগর মাইকেল ফ্যারাডে অবসর পেলেই বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা শুনতেন। পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি রেলস্টেশনের দোকানে কাজ করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়ে সময় ব্যয় করতেন। আসলে সময়ের অপচয় না করে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি যিনি করতে পারেন, তাঁকে মহাকাল স্মরণ করে। তা ছাড়া দেখা যায় পারিবারিক ও সমাজজীবনে সময়কে গুরুত্ব দিলে জীবন সুখময় হয়ে ওঠে।
সমস্ত উন্নতির মূলে থাকে সময়ানুবর্তিতা। সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে জীবন ব্যর্থতা আর অসফলতায় পর্যবসিত হয়-তাই সময় অপচয় একপ্রকার অপরাধ। মনুষ্যজীবন যাতে এই অপরাধে কবলিত হতে না পারে,
তার জন্য চাই বাল্যকাল থেকে সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ। বিশেষ করে ছাত্রজীবনই হল সেই প্রশিক্ষণের যথার্থ ক্ষেত্র। কেন-না মানুষের ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ ফসলের বীজ বপনের প্রত্যাশিত লগ্ন-সার্থক জীবনগঠনের প্রস্তুতি পর্ব। সময়-সচেতন অধ্যয়নই তাকে সাফল্য এনে দেয়। আবার সময়-অচেতন অলস ছাত্র বিফলতার গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পদে পদে ব্যর্থ হয়।
সময়ানুবর্তিতা শুধু আত্মজাগরণই ঘটায় না-সময়ানুবর্তিতা মানুষকে করে তোলে কর্তব্যমুখী, দেশ ও সমাজের প্রতি করে তোলে দায়িত্বশীল। সর্বোপরি সময়ানুবর্তিতা মানুষের মনে জাগ্রত করে মানবিকতাবোধ। শুধু তাই নয়, যে মানুষ সময়নিষ্ঠ, তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে সমষ্টিজীবনের পথে পা বাড়াতে পারেন, আর হয়ে উঠতে পারেন বিশ্বনাগরিক।
‘জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে’- সময়ানুবর্তিতা এই কল্যাণপূত কর্মের গতিপথ প্রশস্ত করে দেয়। বুদ্ধদেব, জিশু খ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ, চৈতন্যদেব, সক্রেটিস, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শেকসপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, মাদার টেরিজা প্রমুখ যাঁরা মানবমুক্তির পথ দেখিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সময়রূপ সম্পদকে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে অমরত্ব অর্জন করেছেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সময়কে অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচনা করে শুভ কর্মপথে নির্ভয়ে পদসঞ্চারে আলোকতীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করা।
৪। [দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না। আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক করিতে হইবে। তোমরা সবল হও, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের সমীপবর্তী হইবে।]
চরিত্রগঠনে খেলাধুলার ভূমিকা : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
প্রাচীনকাল থেকেই খেলাধুলার প্রচলন আছে। শরীর ও মনের সুস্থতার অন্যতম উৎস খেলাধুলা। খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের পাশাপাশি বিশুদ্ধ আনন্দও লাভ করা যায়। তাই খেলাধুলায় শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে। নেতৃত্বশক্তি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মতো গুণের বিকাশ ঘটায়। একটি প্রবাদ আছে,- “All work and no play makes Jack a dull boy”। তাই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ছাত্রজীবন থেকে খেলাধুলাকে বাদ দেওয়া যেমন অপ্রয়োজনীয়, তেমনই অবাঞ্ছিত একটি ধারণা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- “যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গায়িত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্য্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম দেহ, সুস্থ মানসিকতার জন্য খেলাধূলার প্রয়োজন।”
শিক্ষা ও খেলাধুলা এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলার অভ্যাস দেহ ও মনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শাস্ত্রে আছে-“ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ”-অর্থাৎ ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। আর সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে দরকার সুস্থ শরীর, নির্মল মন। শুধুমাত্র পড়াশোনাই যথেষ্ট নয়। তাতে একঘেয়েমি আসে। ছাত্রজীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা সাফল্যের চাবিকাঠি, অন্যতম সহায়ক। তাই পৃথিবীর সবদেশেরই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় খেলাধুলাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের স্কুলগুলিতে দৌড়ঝাঁপ, ড্রিল, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, হা-ডু-ডু, সাঁতার, যোগব্যায়াম, খো-খো প্রভৃতি খেলা অবশ্যকরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; শুধু স্কুল নয়, অনেক উন্নত দেশে কলকারখানায় কাজ শুরু করার আগে ব্যায়ামচর্চা করানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রজীবনে চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, নীতিবোধ, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার মতো সদ্গুণগুলির বিকাশ ঘটে খেলাধুলার মাধ্যমে; যা বাস্তবজীবনে অপরিহার্য মানবীয় গুণ হিসেবে পরিচিত। এর দ্বারা ব্যক্তিজীবন ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়। ‘স্পোর্টসম্যান স্পিরিট’ ভবিষ্যতে জীবনের উত্থানপতনগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা দেয়।
খেলাধুলার মাধ্যমে ক্ষুদ্র, একা, অসহায় অবস্থা কাটানো যায়। – দলবদ্ধভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ, জাতীয়তাবোধ, নেতৃত্বদান, হারজিতের খেলায় শেষ পরিণতিতে বিচলিত না হওয়া, ভীরুতা ও দুর্বলতা দূর করে। – খেলাধুলায় দেশের সাফল্য আমাদের গর্বিত করে। বর্তমান কর্মব্যস্ততার – যুগে আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের থেকে মানসিক পরিশ্রম বেশি হয়। এই – দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি – রোগ দেখা দেবে; যা ছাত্রজীবনে অভিশাপস্বরূপ। তাই খেলাধুলার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।
খেলাধুলা ছাত্রজীবনে অপরিহার্য বলে শুধু খেলায় মনোযোগী হলে পড়াশোনায় ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। পড়া ও খেলা একে অপরের পরিপূরক তাই একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়। অতিরিক্ত খেলাধুলায় শারীরিক ক্লান্তিও যেমন আসে তেমনই পড়াশোনায় আশানুরূপ সাফল্য অর্জন বাধা পায়।
ছাত্রজীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলাধুলাকে শিক্ষার অঙ্গ করে পাশাপাশি অনুশীলন আবশ্যিক করে তুলতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের অঙ্গ হিসেবে খেলাধুলা আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে সুস্থ জীবন, সুস্থ সমাজ, সুস্থ দেশ গঠনের লক্ষ্যে। তাহলে কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলতে পারব-“চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।”
৫। [শ্রেণিতে যেসব বই নিয়ম করেই পড়তে হয়, মাস্টারমশাই যত্ন করেই তা পড়িয়ে দেবেন। এটুকু তো প্রত্যাশিতই। মনকে নিশ্চয় একটু একটু করে শিক্ষিত স্তরে পৌঁছে দেয় সে সব পড়াশোনা। কিন্তু ছোটোদের মনকে অনেকখানি বাড়তি সজীবতা দেয় মাস্টারমশাইদের এই প্রথা ভাঙার সাহস। পাঠ্যরেখার স্থিরতার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি কোনো কিশোর মনকে তাঁরা চালিয়ে দেন কোনো অভাবনীয়ের দিকে, কোনো স্বপ্নের দিকে, কোনো চ্যালেঞ্জের দিকে, তাহলে সে মন হয়তো অনেকদিনের পুষ্টি পেয়ে যায়, পেয়ে যায় কোনো নতুন জগতের আনন্দ।]
নতুন মাস্টারমশাই : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। তাদের সেই বড়ো হয়ে ওঠার পথে তাদের সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে তাদের বাবা-মা। এরপর নির্দিষ্ট বয়সের পরে তারা পা রাখে বিদ্যালয়ের গন্ডিতে। তাদের সামনে উন্মুক্ত হয় বৃহত্তর জগৎ, সান্নিধ্য ঘটে বহু নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পালন করেন তাদের পবিত্র দায়িত্ব, ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ার সুমহান কর্তব্য।
শিক্ষক আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট পরিসরে পাঠ্য-পুস্তকগুলি নিয়মিত পড়িয়ে পাঠ্যবিষয়টির দুরূহতা দূর করতে সহায়তা করেন, সহায়তা করেন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উত্তর লেখার কৌশল রপ্ত করিয়ে অধিক নম্বর পেতে। কিন্তু শিক্ষকের কাজ কি এটুকুতেই সমাপ্ত হয়? তা নয়। পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবহির্ভূত অনেক তথ্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরে তারা তাদের মানসিক সজীবতা বাড়িয়ে তোলেন। তাদের সামনে প্রসারিত করেন অজানা বহির্বিশ্বের নানা রহস্য।
শুধুমাত্র পুথিপাঠ করলেই জীবনে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করা যায় না। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে পাঠ্যবহির্ভূত নানা বিষয়ও তাদের জানতে হয়। তাহলেই তো ঘরের সীমানা অতিক্রম করে মন চলে যেতে পারে সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারের কোনো অচিনপুরে। সেই অচিনপুরে পৌঁছে যাওয়ার পথ কিন্তু দেখান জীবনের পথপ্রদর্শক-ওই মাস্টারমশাই। একারণেই বলা হয় জীবনে গুরুর স্থান সবার উপরে। তিনিই আমাদের জানতে শেখান, চিনতে শেখান, জীবনপথে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র শেখান। সেই চরৈবেতি মন্ত্রের উজ্জীবন শক্তিতে আমরা এগিয়ে চলি।
এমনই এক মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক অমিতবাবু। অমিতবাবুর জ্ঞানের জগৎ ছিল অগাধ। বিদ্যালয়ে তাঁর পড়া শোনার জন্য আমরা সকলে উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা বসে থাকতাম সারাটা ক্লাস। তিনি শুধুমাত্র পাঠ্য কবিতা বা গল্প পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতেন না। একইসঙ্গে তিনি পড়াতেন সেই সাহিত্যিকের অন্যান্য রচনা, যা সাহিত্যিকের কবিমানস বুঝতে আমাদের সহায়তা করত। তিনি আমাদের আলোচ্য সাহিত্য বিষয়টির অনুরূপ অন্যান্য সাহিত্যও পাঠ করাতেন বিষয়বস্তুকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য। অমিতবাবুর শিক্ষাদানের এমন পদ্ধতি আমাকে পরবর্তী জীবনেও উপকৃত করেছে, সবথেকে বড়ো কথা তাঁর পড়ানো আমাকে সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।
একজন শিক্ষকের জ্ঞান অপার। কিন্তু সেই শিক্ষকই যখন নিজের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য গবেষণায় রত হন, তখন তাঁর চিন্তাভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য থাকেন অপর এক শিক্ষক-গবেষক।
তাই শিক্ষক শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ের দুরুহতা বোঝানোরই কান্ডারি নন। তিনি কিশোরমনকে চালিত করেন কোনো অভাবনীয়ের দিকে। শিক্ষার্থীদের মনে তিনিই বপন করেন ভবিষ্যতের স্বপ্নের বীজ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই গড়ে দেন আগামী দিনের এগিয়ে চলার লড়াকু মানসিকতা। এ সমস্ত কিছুর ফলে ছাত্রমন সজীব হয়ে ওঠে, নতুন জগতের এক অনাস্বাদিত আনন্দ লাভকরে, লাভ করে মানসিক সজীবতা; যা তাদের সারাজীবন পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকে। এ কারণেই শিক্ষক আমাদের কাছে নমস্য। আমাদের প্রাণের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁদের প্রতিই নিবেদিত।
৬। [বাংলায় বিজ্ঞানচর্চায় নানারকম বাধা আছে। বাংলায় পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের উদ্যোগ সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এদেশের জনগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও নগণ্য। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকলেও বিজ্ঞান বিষয়ে তাদের ধারণা খুবই সামান্য। বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত হতে না পারলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।]
বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা : প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা
বিজ্ঞানচর্চা হল যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণের দ্বারা কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা এবং সেই সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি কী হবে, কোন্ ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হবে- তা নিয়ে বিস্তর মতভেদের অবকাশ আছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মতো স্বাধীন দেশসমূহে ঔপনিবেশিক শাসকেরা রাজত্ব চলাকালীন জনগণের ভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার অনুপযুক্ত বলে প্রচার করেছে। ফলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে একধরনের হীনম্মন্যতাবোধ তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করা যায় কিনা তা নিয়ে। কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থই ইংরেজি ভাষায় রচিত। এ বিষয়ে আলোচনা প্রতিনিয়তই চলেছে।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বই-কি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই।’ মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিশ্বে ফ্রান্স, জাপান, রাশিয়া, চিন, জার্মান ইত্যাদি প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগণ্য দেশগুলি বিজ্ঞানচর্চা-সহ সর্বস্তরের বিদ্যাচর্চায়
মাতৃভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্তর মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞরা প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাতেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্রও ছিল তৎকালীন সাহিত্যভাষাতেই।
আধুনিক বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল বাংলা অক্ষর তৈরির পরেই। শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়ম কেরি, মার্শম্যান প্রমুখের অনূদিত নানা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশ এবং উইলিয়ম কেরির পুত্র কেলিক্স কেরি অনূদিত চিকিৎসাশাস্ত্র ‘বিদ্যাহারাবলী’র নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। পাশাপাশি ‘বিজ্ঞান সেবধি’, ‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ‘জ্ঞানান্বেষণ’ নামক পত্রিকাগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ ছাড়াও অক্ষয় কুমার দত্তের ‘পদার্থবিদ্যা’ প্রবন্ধগ্রন্থটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধের অন্যতম গ্রন্থ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে বিজ্ঞানের দুরুহ রহস্যকে শিল্পসুষমামণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন।
সাম্প্রতিককালে ‘বিজ্ঞানবার্তা’, ‘কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান’, ‘কিশোর ভারতী’ ইত্যাদি পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে নানা আলোচনা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার বহু ভাষাভাষী আমাদের দেশে ভাষা সমস্যার জন্য বিজ্ঞানচর্চা সেভাবে উন্নতি ও প্রসার লাভ করতে পারেনি। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার মুখোমুখি হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যই আজও বিজ্ঞান অপরিচয়ের আড়ালে রহস্যমণ্ডিত হয়ে থাকছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করা যায় না।
বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রতিকূলতাও অনেক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন নামের পারিভাষিক শব্দের অভাব আছে বাংলায়। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলেও সেভাবে সাফল্য পায়নি। কিন্তু বর্তমানে সে কাজে হাত দিয়েছে ‘বিজ্ঞান পরিষদ’। মনে রাখা দরকার বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার অভাবে সাধারণ জনগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খুবই নগণ্য। ফলে উপযুক্ত পরিভাষার খুবই প্রয়োজন। পাশাপাশি ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনও আছে। যাতে আন্তর্দেশীয় পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে অসুবিধা না হয়। এই সমস্যার সমাধান করতে পারে উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ এবং সর্বজনপাঠ্য সহজ-সরল ভাষার অথচ শিল্পসুষমামন্ডিত প্রবন্ধ। তাই একাজে পারদর্শী এমন কিছু তরুণ গবেষকদের প্রচেষ্টা একান্ত কাম্য। কারণ ভাষা যদি আড়ষ্ট হয়, রচনা যদি কেবলই আক্ষরিক অনুবাদ হয়- তবে তা কখনোই হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না।
যুগের প্রয়োজনে কোনো প্রতিকূলতাই চিরস্থায়ী হয় না। আপন প্রয়োজনে, নিয়মে তার পথ নির্ধারিত হয়। বাংলা ভাষায় যদি দর্শন, অর্থনীতির চর্চা হতে পারে তবে সে ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা না হওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না। তাই দরকার অনুশীলনের। সর্বোপরি উৎসাহ ও নিষ্ঠার। – হয়তো সেদিন খুব বেশি দূরে নেই যেদিন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় কোনো প্রতিবন্ধকতাই থাকবে না।