আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : মূল ধারণা এবং রাজনৈতিক মতবাদসমূহ প্রশ্ন উত্তর | ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম অধ্যায় প্রশ্ন উত্তর | International Relations question answer | Class 12 4th Semester Political Science First Chapter question answer
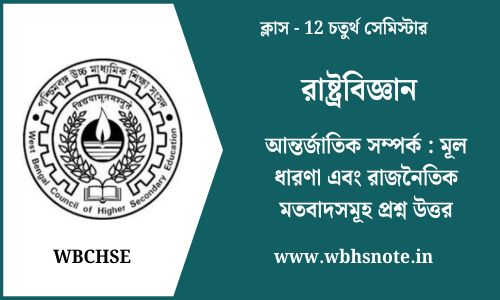
১। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য:
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।
পরিধিগত পার্থক্য : বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সম্পর্কের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি অরাষ্ট্রীয় নানান সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের আলোচনাও করে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বসমাজের অন্তর্গত সকল জনগণ ও গোষ্ঠীর সব সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। মূলত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক বিষয়গুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক পরিবেশ-সহ বিষয়গুলিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো ব্যাপক ধারণা নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কূটনীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবল রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করে।
প্রকৃতিগত পার্থক্য: প্রখ্যাত বাস্তববাদী তাত্ত্বিক মরগেনথাউ মনে করেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ ও সংঘর্ষকেন্দ্রিক আলাপ-আলোচনা।
তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, মিত্রতা ও সমন্বয়সাধন ইত্যাদি বিষয়কে বোঝায় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমুখী অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বিষয়ের তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিক নিয়ে আলোচনা করে।
পামার ও পারকিন্স-এর মত: পামার ও পারকিন্স-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় ব্যাপক। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল ‘আন্তর্জাতিক সমাজের রাজনীতি’ যা মূলত কূটনীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বসমাজের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীগুলির সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংশবিশেষ।
শ্লেইচার-এর মত : শ্লেইচার মনে করেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমার্থক নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও সহযোগিতা দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করে।
অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধানত বিরোধ, বিবাদ ও সংঘর্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
কে জে হলটি-এর মত : হলস্টির মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, বিদেশনীতি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক নীতি-নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।
তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি উপরোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটি সাধারণত পররাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা তথা সরকার বা উচ্চতর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে।
মরগেনথাউ-এর মত: মরগেনথাউ-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার বিষয়বস্তুতে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ক্ষমতার বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা এমনকি সমন্বয় সাধনের বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
তবে তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল মূলত ক্ষমতার লড়াই। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করে।
২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের ধারা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের ধারা:
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।
(i) জাতিরাষ্ট্রের উৎপত্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ: ইউরোপের নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানরা ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির বক্তব্য হল, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এভাবে প্রথম আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সূচনা হয়।
(ii) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ: ১৯১৪-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও মারণক্ষমতা রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধ এড়ানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। সাধারণ জনগণও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা যুদ্ধের কারণ হিসেবে গোপন কূটনীতিকে দায়ী করে ও যুদ্ধবিরোধী জনমত গড়ে তোলে। এই সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের দাবি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন স্থায়ী শাস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। চোদ্দো দফা দাবি পেশ করেন। যার বাস্তবায়ন ঘটে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা লক্ষ করা যায়।
(iii) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী ভয়াবহতার ফলে বিশ্বরাজনীতির আমূল পরিবর্তন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিন্যাসে নতুন মাত্রা এনে দেয়। এই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ পুনরায় শান্তিকামী হয়ে ওঠে। এই পর্বে সৃষ্টি হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। এই পর্বেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বতন্ত্র পাঠ্যবিষয় হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে বিষয়টিকে নিয়ে আবর্তিত হয় তা হল ঠান্ডা লড়াই। এইরকম পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে।
(iv) সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ: নব্বইয়ের দশকের পর বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিমেরুতার অবসান ঘটার ফলে শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। ফলস্বরূপ সারা বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিন্যাসের এই পরিবর্তনকে একমেরু বিশ্ব বলে অভিহিত করা হয়। মূলত নব্বই-এর দশকে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিকশিত করেছে। এরপর একুশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সারা বিশ্বে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে যাওয়া।
পরিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙিনা থেকে বেরিয়ে পঠনপাঠনের শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভকরেছে-যা সমাজবিজ্ঞানের নবীন শাস্ত্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৩। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় আদর্শবাদ বলতে কী বোঝো? তত্ত্বটির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।
আদর্শবাদের সংজ্ঞা
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় সেই বিশ্লেষণভঙ্গিকে যা স্থায়ী বিশ্বশান্তি, যুদ্ধের অবসান, নৈরাজ্যের অবসান ও যৌথ নিরাপত্তার বিষয়কে লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরে এবং মানবপ্রকৃতির শান্তিকামী প্রবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
আদর্শবাদী তত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:
সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আদর্শবাদী তত্ত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা যায়-
(i) নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব: আদর্শবাদে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা (Morality)-কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ বিশ্বসম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। ফলে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে যুদ্ধ, সহিংসতা, স্বৈরাচার প্রভৃতিকে এড়ানো যায়।
(ii) পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব: আদর্শবাদী তত্ত্ব রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক স্থাপনে পারস্পরিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার রেষারেষি থাকলে যুদ্ধমুক্ত শান্তিপূর্ণ আদর্শ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে।
(iii) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: আদর্শবাদের তাত্ত্বিকগণের মতে, যুদ্ধের পরিস্থিতিকে নির্মূল করতে ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উপস্থিতি থাকা দরকার। তাঁরা মনে করতেন, আন্তর্জাতিক স্তরে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নৈরাজ্যমূলক অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফেরানোর জন্য মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া) উদ্যোগে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি ‘লিগ অফ নেশনস্’-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
(iv) কূটনীতি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা : আদর্শবাদীরা আলাপ-আলোচনার সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মীমাংসার মাধ্যমে যুদ্ধকে নির্মূল করে স্থায়ী শাস্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। তাঁরা কোনোরকম সহিংসতা, ক্ষমতা প্রদর্শন বা সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসাকে অনুমোদন করে না।
(v) রাষ্ট্রীয় কারকের প্রাধান্য: আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ‘রাষ্ট্র’ হল বিশ্বব্যবস্থার প্রধান কারক (Actor) বা ক্রিয়াকারী। কারণ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনার প্রধান চালিকাশক্তি।
(vi) ইতিবাচক মানবচরিত্র: আদর্শবাদীদের মতে, মানবপ্রকৃতি মূলত ভালো ও সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন। মানবচরিত্র আত্মকেন্দ্রিক বা ক্ষমতালিঙ্গু নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্যের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এই সহযোগিতার মানসিকতাই মানবসভ্যতা উন্নয়নের মূল উৎস।
উপসংহার: তবে ১৯৩০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য, ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান, ক্ষমতার রাজনীতির আধিপত্য, অর্থনৈতিক মন্দা, স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সংশয় প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় আদর্শবাদের অকার্যকারিতা ও দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তোলে।
৪। বাস্তববাদ সম্পর্কে মরগেনথাউ-এর বিশ্লেষণ আলোচনা করো।
বাস্তববাদ সম্পর্কে মরগেনথাউ-এর বিশ্লেষণ
সাবেকি বা রাজনৈতিক বাস্তববাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন হ্যানস্ মরগেনথাউ। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘পলিটিক্স অ্যামঙ্গ নেশনস্: দ্য স্ট্রাগল ফর পাওয়ার অ্যান্ড পিস’ গ্রন্থে বাস্তববাদী তত্ত্বের ছয়টি মূল নীতির উল্লেখ করেন। এগুলি বাস্তববাদের মূল স্তম্ভ হিসেবে গৃহীত হয়। নীতিগুলি হল-
(i) রাজনীতি বস্তুগত বিধি দ্বারা চালিত: মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুগত বিধিনিয়ম (Objective laws) দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হয়। এই বিধিনিয়মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক আচরণকে বোঝা সহজ হয়।
(ii) জনতা ও জাতীয় স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক: মরগেনথাউ-এর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। এজন্যই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হল জাতীয় স্বার্থ। তবে ক্ষমতা ছাড়া জাতীয় স্বার্থ পূরণ অসম্ভব। যেহেতু জাতীয় স্বার্থকে পূরণ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন সেহেতু জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
(iii) জাতীয় স্বার্থের ধারণা পরিবর্তনশীল : বাস্তববাদীদের মতে, স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় স্বার্থের ধারণা পরিবর্তিত হয়। আজ যেটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা নাও থাকতে পারে। ফলে রাষ্ট্রগুলিকে তাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে হয়।
(iv) সর্বজনীন নৈতিক বিধির অনুপস্থিতি: নৈতিক বিধির সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তববাদের সূক্ষ্ম বিরোধ আছে, তবে এটি নৈতিকতাবিরোধী নয়। মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্রের কাজকর্মে কোনো সর্বজনীন নৈতিক ধারণাকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তিনি নৈতিকতার বদলে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বরং বিশ্বজনীন নীতিবোধগুলি যতটুকু বিদেশনীতির সঙ্গে বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তা যাচাই করে গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন।
(v) কোনো জাতির নৈতিক আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন নয় : মরগেনথাউ মনে করেন, প্রত্যেক জাতি একটি বিশেষ নৈতিক আকাঙ্ক্ষা থাকে যা সেই দেশের বিদেশনীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তাই কোনো একটি রাষ্ট্রের নৈতিক ধারণাকে বিশ্বজনীন নৈতিকতার সঙ্গে একাত্ম করা উচিত নয়। অর্থাং কোনো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বা জাতীয় স্বার্থ কখনোই সর্বজনীন হতে পারে না।
(vi) রাজনৈতিক বাস্তববাদের স্বতন্ত্রতা : মরগেনথাউ রাজনীতি শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের জোরালো দাবি তুলেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতির সঙ্গে জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক থাকলেও ক্ষমতার আলোয় বর্ণিত জাতীয় স্বার্থের ধারণা রাজনীতিকে অন্যান্য চিন্তাবিদ্যা থেকে পৃথক করেছে।
উপসংহার: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী আলোচনা বহুতাত্ত্বিক হয়ে থাকলেও মরগেনথাউ-এর অবদান সর্বাধিক শাস্ত্র অধ্যয়নে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।
৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব হিসেবে বাস্তববাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।
ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে (১৯৪৫ খ্রি.) অর্থাৎ ঠান্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বাস্তববাদ জোরালো তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাস্তববাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবক্তা হলেন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস্ মরগেনথাউ।
সংজ্ঞা: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্ব বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায়, বস্তুজগতে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান বা বিরাজমান, তাকে স্বীকার করে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। অর্থাৎ ব্যক্তি বা সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ বা কর্মসূচি প্রণয়ন করার পিছনে কল্পনার থেকে বাস্তব অবস্থা যখন প্রকৃত চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে তখন তাকে বাস্তববাদ বলা হয়।
বাস্তববাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:
সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা যায়। এগুলি হল-
(i) রাষ্ট্রাকন্দ্রিকতা: বাস্তববাদী তত্ত্ব অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। রাষ্ট্র হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু।
(ii) মানবচরিত্রের নেতিবাচক বিশ্লেষণ: বাস্তববাদীদের মতে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ক্ষমতালোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অসাধু এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক রাজনীতিও ক্ষমতা ও চির সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
(iii) ক্ষমতার গুরুত্ব: বাস্তববাদীরা মনে করে, ক্ষমতা হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ ‘ক্ষমতা’-ই রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থ পূরণে সহায়তা করে। কোনো রাষ্ট্র কতটা ক্ষমতাশালী তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওই রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্ধারিত হয়।
(iv) সামরিক শক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান: নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাষ্ট্রগুলির প্রাথমিক কর্তব্য বা দায়িত্ব হল সামরিক শক্তিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা। বাস্তববাদীদের কাছে সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
সমালোচনা
বাস্তববাদী তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভকরলেও তত্ত্বটি নানা সমালোচনার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল-
(i) অরাষ্ট্রীয় কারককে উপেক্ষা : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র অন্যতম প্রধান কারক একথা সঠিক। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বে রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য অরাষ্ট্রীয় সংগঠন বা কারকগুলির কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির গুরুত্বও নেহাত কম নয়। ১৯৬০-এর দশক থেকে বিশ্বরাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তারা রাষ্ট্রের মতো সমানভাবে সক্রিয় থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির আঞ্চলিক জোটের কথা বলা যায়।
(ii) মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা: মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তববাদীদের ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। মানবপ্রবৃত্তি সর্বদা ক্ষমতালিঙ্গু বা দ্বন্দ্বপ্রিয় নয়, পারস্পরিক সহযোগিতাও মানবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।
(iii) অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে উপেক্ষা : মরগেনথাউ তাঁর তত্ত্বে কেবলমাত্র রাষ্ট্রগুলির সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সামরিক ক্ষমতা ছাড়াও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ক্ষমতাও যে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে মরগেনথাট্ট তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।
উপসংহার: উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, বাস্তববাদ ‘ক্ষমতা’-র ধারণাকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নির্ণায়ক বলে ব্যাখ্যা করেছে, যা সর্বাংশে সত্য। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য আজও বাস্তব। এ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের ধারণাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বাস্তববাদীরা প্রথম তুলে ধরেন।
৬। উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উদারনীতিবাদী তত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
১৯৭০-এর দশকে বাস্তববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় উদারনীতিবাদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-
(i) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা: উদারনীতিবাদ ক্ষমতার রাজনীতি, হিংসা ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিশ্বরাজনীতিকে মুক্ত করে, যুদ্ধকে পরিহার করে আন্তর্জাতিক সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এজন্য তাঁরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক আইন মান্য করা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
(ii) অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির প্রাধান্য: উদারনীতিবাদীগণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের পাশাপাশি অরাষ্ট্রীয় কারকসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনগুলি জাতিরাষ্ট্রের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। যেমন-বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি বা Multinational Corporation (MNC) বাস্তবে অনেক দেশের সরকার অপেক্ষাও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
(iii) গণতন্ত্রের প্রসার : এই তত্ত্ব বিশ্বব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারের কথা বলে। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুদ্ধ-বিবাদের পরিবর্তে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনকি উদারনীতিবাদীদের মতে, রাষ্ট্রগুলি যদি একই আদর্শের উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাহলে তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, রেষারেষি, যুদ্ধ ও যুদ্ধের হুমকি প্রভৃতির অবসান ঘটবে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, বিশেষত অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে।
(iv) আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্ব : এই তত্ত্ব সামরিক উন্নয়নের পরিবর্তে দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রসারের উপর জোর দেন। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মতে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন এবং অবাধ বাণিজ্য নীতির পথ ধরে বহুপাক্ষিক (Multilateral) অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলির আর্থিক প্রগতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব।
(v) ক্ষমতার রাজনীতিকে অস্বীকার: উদারনীতিবাদ ক্ষমতার রাজনীতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের মতে, ক্ষমতার রাজনীতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, রেষারেষি, সংঘর্ষ এমনকি যুদ্ধকে ডেকে আনে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ক্ষমতা সম্পর্কিত বাস্তববাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় উদারনীতিবাদ স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে গড়ে উঠেছে।
(vi) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা: উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্তরে যৌথ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে উদারবাদীরা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার উপর জোর দেয়।
(vii) বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা: উদারনীতিবাদী তত্ত্ব জাতিরাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ভেদাভেদকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি ও সুস্থিতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারনীতিবাদী তত্ত্বকে উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে অভিহিত করা হয়।
উপসংহার: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় উদারনীতিবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তত্ত্বটি অধিকমাত্রায় পাশ্চাত্যনির্ভর হওয়ায় একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি বলে সমালোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সমালোচকদের মতে পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তারের যে ধারণা উদারবাদীগণ দিয়েছেন তা বিশ্বব্যাপী বৈষম্যকে বৃদ্ধি করেছে।
৭। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মার্কসবাদ-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় মার্কসীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:
কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ ধারা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় মার্কসীয় তত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল-
(i) অর্থনৈতিক উপাদানের প্রাধান্য: মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অর্থনৈতিক উপাদানই হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান উপাদান। আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ, সংগ্রাম সংঘটিত হয় তার প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ভিত্তি (Base) এবং আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতি, রাজনীতি হল উপরিকাঠামো (Super Structure)। আন্তর্জাতিক স্তরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের সময় বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্কটি (উন্নত দেশগুলি কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন) প্রতিফলিত হয়।
(ii) আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণি চরিত্রের গুরুত্ব: মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার মূল উপাদান হল ‘শ্রেণি’। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রেণিভিত্তিক আলোচনার উপরেই আস্থা রেখেছিলেন।
(iii) শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্ব: মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বরাজনীতিকে বিশ্লেষণ করে শ্রেণিসংগ্রামের আলোকে। মার্কসবাদীদের মতে, সারা বিশ্ব ‘haves’ এবং ‘have nots’-এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এর মূলে আছে পুঁজিবাদী বিশ্ব বাজার দখল বা বিস্তারের ছলে দরিদ্র দেশগুলিকে শোষণ করার লোভ। যার প্রকাশ ঘটে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার অসম বিন্যাসের মধ্যে।
(iv) সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাধাজ্যবাদের বিরোধিতা: মার্কসবাদ অনুসারে ধনতন্ত্রবাদের প্রসারিত রূপ হল সাম্রাজ্যবাদ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দখল করে বিশ্ব বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করা। এরই আধুনিক রূপ হল নয়া সাম্রাজ্যবাদ। মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন, যুদ্ধ সবকিছুর মূলে আছে আর্থিক শোষণ। তাই মার্কসবাদ যাবতীয় আর্থিক শোষণের অবসান চায়।
(v) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার : তৃতীয় বিশ্বের অবদমিত জাতিগুলির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন, স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ পতনের পর শ্রেণিহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে। কারণ এরূপ শ্রেণিহীন, রাষ্ট্রহীন ব্যবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে না।
(vi) সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ : মার্কসবাদী দর্শন অনুসারে, সর্বহারাদের কোনো দেশ নেই, সর্বত্রই এই শ্রেণি শোষিত ও অবদমিত। তাই পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বহারা শ্রেণিকে বিপ্লবের ডাক দিতে হবে। বিশ্ববিপ্লব সম্পাদনের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণির মুক্তি ঘটবে বলে এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা মনে করেছিলেন।
(vii) বিশ্ববিপ্লবে গুরুত্বদান: মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা আন্তর্জাতিক স্তরে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এনে বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সমাজতন্ত্রবাদই তাদের কাছে আদর্শব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে যুদ্ধ, সংঘাতের অবসান ঘটবে বলে মনে করা হয়।
উপসংহার: আন্তর্জাতিক স্তরের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মার্কসবাদের উদ্ভব হলেও তত্ত্বটি অতিমাত্রায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের দোষে দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তত্ত্বটি যে বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ধনতন্ত্রের জয়যাত্রায় সেই স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে।