দিগ্বিজয়ের রূপকথা কবিতার বিষয়বস্তু ক্লাস 12 তৃতীয় সেমিস্টার বাংলা | Digwijoyer Rupkotha Kobitar Bishoybostu
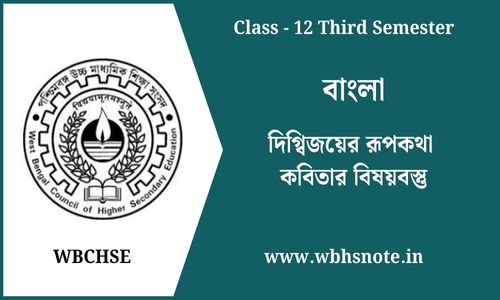
উৎস
‘দিগ্বিজয়ের রূপকথা’ ১৯৭৩ সালে রচিত। এটি ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’ কাব্যের অন্তর্গত। পরবর্তীতে কবিতাটি ‘নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থে স্থান পায়।
প্রেক্ষাপট
কবি নবনীতা দেবসেন তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯) বইটির ভূমিকায় বলেছেন-
“তিনভাগে কবিতাগুলিকে সাজানো হয়েছে। প্রথমভাগে আছে ১৯৫৭-৫৯-এ লেখা, ১৯৫৯-এ প্রকাশিত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম প্রত্যয়’ থেকে নেওয়া কবিতা, দ্বিতীয়ভাগে ১৯৫৯-৭১-এ লেখা, ১৯৭১-এ প্রকাশিত আমার দ্বিতীয় কবিতার বই ‘স্বাগত দেবদূত’-এর কিছু কবিতা, আর তৃতীয়াংশে সবই অগ্রন্থিত (কিন্তু প্রকাশিত) কবিতা। ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’ নামে একটি বই বেরনোর কথা ছিল ১৯৭৫ নাগাদ, আমারই আলস্যে বের হতে পারেনি।”
‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সংকলন গ্রন্থটির শেষে গ্রন্থ বিভাজন করে পূর্বোক্ত দুটি বই ছাড়াও আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। যেমন- ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’, ‘লায়নটেমারকে’, ‘১৯৯৬-২০০২’, ‘তুমি মনস্থির করো’। ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’ শিরোনামে পরিকল্পিত গ্রন্থেই কবি আলোচ্য কবিতাটি রেখেছেন। নবনীতা তাঁর নিজস্ব রূপকথার গল্পগুলিতে দেশ-বিদেশের প্রচলিত রূপকথার ছাঁচ গ্রহণ করলেও শিশু-মনস্তত্ত্বের কথা ভেবে, আধুনিক কালের শিশুদের কথা ভেবে কোনো নিষ্ঠুরতা ও নেতিবাচকতাকে স্থান দেননি। সেইসব রূপকথার প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে রচনা করেছেন ‘দিগ্বিজয়ের রূপকথা (১৯৭৩) কবিতাটি। উক্ত কবিতাটিকে তাঁর রূপকথা সমগ্রের নির্যাস বলা যায়। ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’ -এই প্রথম বাক্যটিই বুঝিয়ে দেয়, ‘আমি’ পুরুষ হই বা নারী, আমার রক্তে রাজপুত্রসুলভ শৌর্য ও ঐশ্বর্য বিরাজ করছে।
নবনীতা দেবসেন ‘রূপকথা সমগ্র’ প্রবন্ধের মুখবন্ধে লিখেছিলেন- “আমার সবচেয়ে ভালো লাগত মায়ের কোলে বসে মায়ের মুখে রূপকথা শুনতে।” তিনি আরও বলেন, “বাংলাতে রূপকথা পড়া আমার আজও ফুরোয়নি। রূপকথা তো চিরকালের জিনিস। আমি পড়তে যত ভালোবাসি, রূপকথা লিখতেও ততই আনন্দ পাই। আমি আমার লেখক জীবনের সবচেয়ে শান্তি পেয়েছি কবিতা লিখে, আর সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি শিশুদের জন্য রূপকথা লিখে।”
হ্যাঁ, রূপকথার গল্পের প্রতি প্রায় সব মানুষেরই আকর্ষণ থাকে। বিশেষ করে, শিশু-কিশোরেরা রূপকথার গল্পের মধ্যে নিজেদের কল্পনাকে প্রসারিত করে দেয়। দেশ-বিদেশের এমনই রূপকথার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভা নবনীতা দেবসেনের। তাই তাঁর সাহিত্য সাবালকত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায়শই বিচরণ করেছে ‘দত্যি-দানব-রাজপুত্র’-এর গা ছমছমে রাজ্যে। তিনি যেন শিশু-কিশোরদেরই মনের মতো হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন বেশি। তবে তাঁর সাহিত্য, বৈচিত্র্যের যে বৃহৎ জগতে আনাগোনা করেছে জীবনভর, তার একটা বিশেষ প্রান্ত জুড়ে ছিল নারীদের অন্তরালবর্তী প্রান্তর থেকে বহির্বিশ্বে বার করে এনে সমানাধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার লড়াই।
ইতিহাস যতই নারী জাগরণের অধ্যায় লিখুক পাতার পর পাতা জুড়ে, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতাবিধান তো দূরের কথা, নারীদের শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাওয়াও হয়ে দাঁড়িয়েছে কঠিন কাজ। নবনীতা দেবসেনের নারীবিশ্ব তাই যেন এগিয়ে এল বুদ্ধদেবের সেই বাণী নিয়ে, সমাজের উদ্দেশে, পশ্চাদপর, কুণ্ঠিত মেয়েদের উদ্দেশে বলে উঠল- ‘আত্মদীপো ভব, আত্মশরণ্যে ভব, অনন্যে শরণ্যে ভব’-অর্থাৎ ‘নিজেকে প্রদীপ করে তোলো, নিজেরই শরণ নাও, অপর কোনো মানুষের শরণ নিও না।” কিন্তু আলোচ্য কবিতার নাম তো ‘দিগ্বিজয়ের রূপকথা’-সেখানে নারীবাদের আলোচনা কেন? তার উত্তর লুকিয়ে কবিতার প্রথম কথাটিতেই- ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’।
কবি নবনীতা ইচ্ছে করলেই পারতেন চিরাচরিত রূপকথার গল্পের মতো অনাম্নী দুয়োরানির কোনো রাজপুত্রের নামোল্লেখ করে, তাকে দিগ্বিজয়ে পাঠাতে। কিন্তু তার পরিবর্তে কবিতার বয়ান জুড়ে থেকে গেল এক ‘আমি’। সেই ‘আমি’-ই চলেছে দিগ্বিজয়ে। যে সাহিত্যিক বারংবার নারী-পুরুষের বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবতার দৃষ্টিতে পুরাণপ্রাচীন সব রূপকথার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন-তাঁর সেই রূপকথায় কেবল দুয়োরানির রাজপুত্র নয়, রাজকন্যাও উধাও হবে দিগ্বিজয়ে সেটাই স্বাভাবিক।
“মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা রাজদণ্ডনীতি।”-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’-র আত্মমহিমা, আত্মপ্রত্যয়েই যেন বিনির্মাণ ঘটেছে নবনীতা দেবসেনের রূপকথার রাজকন্যাদের। কবচকুণ্ডল নয়, ধনুকতৃণীর নয়, শিরস্ত্রাণ নয় বরং দুঃখিনী দুয়োরানির আশীর্বাণীকে পাথেয় করে কবিতায় সেই ‘আমি’-র অস্ত্র হয় মস্তিষ্ক আর অন্তরের সম্পদ-বিশ্বাস এবং ভালোবাসা। পুরুষতান্ত্রিক আটপৌরে জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে কবি তাঁর নারীকে দাঁড় করিয়েছেন পুরুষদের সঙ্গে একই সারিতে। তাঁর রূপকথার জগতে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরী থেকে রাজপুত্রকে উদ্ধার করে আনে নারীরা। তাঁর নারী অসময়ের চোখে, অন্যায়ের চোখে চোখ রেখে বলে-
“আমাকে নেবাতে পারে এতো শক্তি রাখে না সময়। কখনো ভেবোনা আমি সময়ের মুখ চেয়ে থাকি। সময় আমার সঙ্গে খেলে যাক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। যতোই কাড়ুক শাড়ি, লজ্জাবস্ত্র ঠিক থাকে বাকি, মন্ত্রবলে বেলা হয়ে যাবে সব, যা ছিলো অবেলা।”
বিষয়বস্তু
নবনীতা দেবসেন দেশ-বিদেশের চিরকালীন রূপকথার বাইরে এসে আধুনিক মন ও মানসিকতা থেকে জাত অভিনব রূপকথার গল্প লিখেছেন। সেইসব গল্পের মূল ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর ‘দিগ্বিজয়ের রূপকথা’ কবিতাটিতে।
আলোচ্য কবিতায় তিনি প্রচলিত রূপকথার প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বক্তব্যকে উৎকৃষ্ট মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। রূপকথার গল্পে দু-ধরনের রানির উপস্থিতি দেখা যায় সুয়োরানি ও দুয়োরানি। সুয়োরানি সুখে থাকে, রাজার মনোযোগ পায় অন্যদিকে দুয়োরানির জীবন অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনাময়। সেই দুয়োরানির পুত্রই একদিন দিগ্বিজয় করে এসে মাকে দুঃখমুক্ত করে। কবি যেন তেমনই এক দুয়োরানির সন্তান। কিন্তু বিষয়বস্তু আলোচনার সর্বাগ্রে বলি, রূপকথার চিরাচরিত জগতের বিনির্মাণ ঘটাতে কবিতার কোনো অংশেই কবি-কথকের কোনো লিঙ্গভেদ চোখে পড়ে না।
কোনো এক অনাম্নী ‘আমি’, প্রথমেই উচ্চারণ করে ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’। বলা বাহুল্য, নবনীতার এই ‘আমি’ আত্মপ্রত্যয়ী এক নারীকণ্ঠ হওয়া অসম্ভব কিছু না। বহির্বিশ্বের আনাচেকানাচে সে তার সমানাধিকার বুঝে নিতেই যেন বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে। তাঁর শিরায়-ধমনিতে রাজরক্ত বইছে। তাঁকে দিগ্বিজয়ে যেতে হবে। কিন্তু রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাজপোশাক, অস্ত্রশস্ত্র তাঁর নেই। সুরক্ষাকবচ, তিরধনুক, শিরস্ত্রাণ কিছুই নেই। দুয়োরানি, কবির দুঃখিনী জননী কেবল দুটি সম্বল দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে ছিলেন। সেই দুটি আশীর্বাদি সরঞ্জাম নিয়ে কবি বের হলেন দিগ্বিজয়ে।
কবিতায় উল্লিখিত দুটি আশীর্বাদি ঐশ্বর্য হল-জাদু-অশ্ব এবং অসি। অশ্ব, কিন্তু আদতে অশ্ব নয়। তা মরুপথে হয়ে যায় উট, আকাশে পুষ্পকরথ, সমুদ্রে সপ্তডিঙা আর তেপান্তরে পক্ষীরাজ ঘোড়া। কবি যখন এই জাদু-অশ্বের নাম রাখেন বিশ্বাস, তখন বোঝা যায় এখানে ঘোড়া হল বিশ্বাসের প্রতীক।
এভাবেই অসি হয়ে উঠেছে ভালোবাসার প্রতীক। যে তরবারি ‘হৃদয়ের খাপে ভরা’, ‘মন্ত্রপূতঃ’, শানিত ইস্পাতখণ্ডের মতো দৃঢ়, ‘অভঙ্গুর’-নাম তার ‘ভালোবাসা’। মন ও মননের এ দুটি সম্পদ যার আছে, সে তো দিকে দিকে জয়লাভ করবেই, সে প্রকৃত অর্থে রাজপুত্র হোক বা রাজকন্যাই হোক।
কবি তাই দৃঢ় আস্থা রেখেছেন যে, ‘বিশ্বাস’ ও ‘ভালোবাসা’ নামক দুটি অক্ষয় সরঞ্জামের সাহায্যেই তিনি পৌঁছে যাবেন তৃয়াহারী খেজুর গাছবেষ্টিত স্বপ্নদ্বীপে-যা কবির কাঙ্ক্ষিত মরূদ্যান।
আরও পড়ুন : আদরিণী গল্পের MCQ প্রশ্ন উত্তর
আরও পড়ুন : অন্ধকার লেখাগুছ MCQ প্রশ্ন উত্তর
আরও পড়ুন : দিগ্বিজয়ের রূপকথা কবিতার MCQ